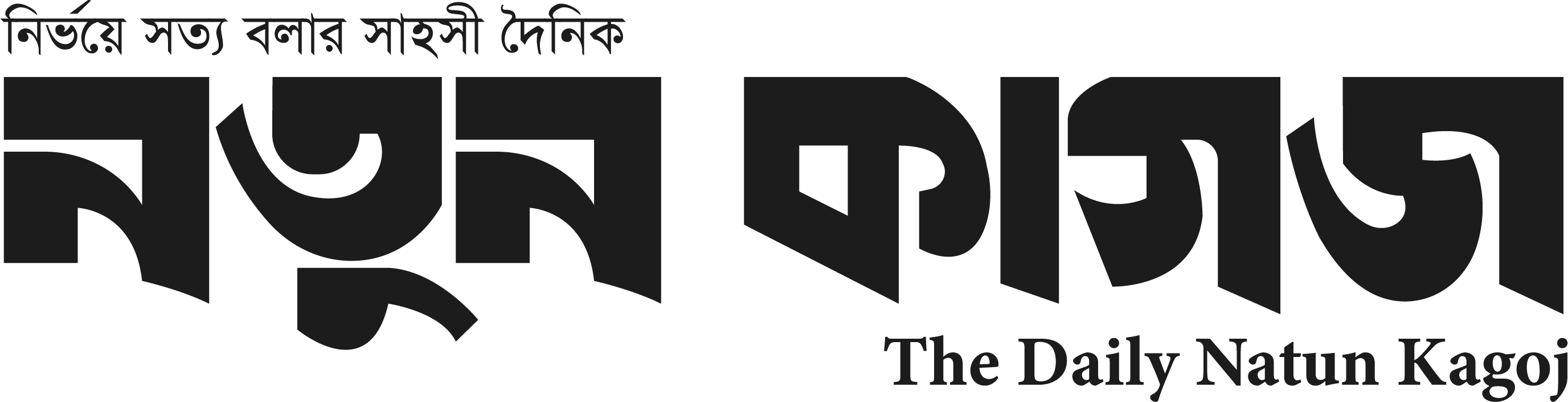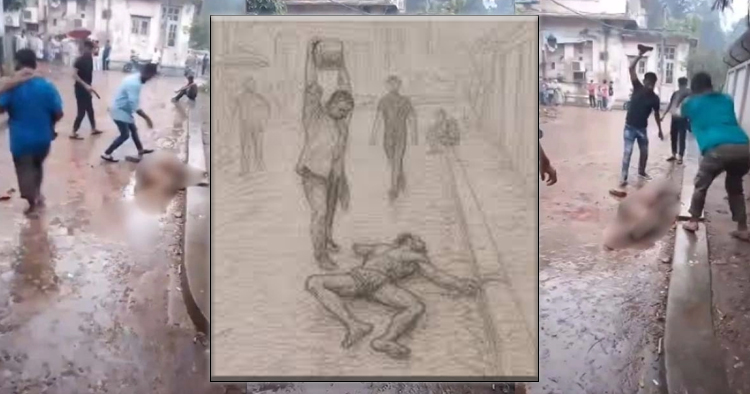নির্বাচনের সামনে আবার সন্দেহ-সংশয়ের ছায়া

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা যেন কিছুতেই কাটছে না। লন্ডনে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের যৌথ ঘোষণা পরবর্তী রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বস্তির আভাস দেখা গেলেও, সেই আশার জায়গাটিও এখন আবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে কি না এ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও নতুন করে সন্দেহ, সংশয় ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।
যেখানে বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলো নির্বাচনমুখী কর্মসূচি চালাচ্ছে, এনসিপি ও অন্যান্য ছাত্রনেতৃস্থানীয় গোষ্ঠী মাঠে সক্রিয় রয়েছে, সেখানে নির্বাচন কমিশন বা সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দেশনার অভাব পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে। লন্ডন বৈঠকের তিন সপ্তাহ পার হলেও নির্বাচন কমিশন এখনও সরকারের কাছ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বার্তা বা নির্দেশনা পায়নি, এমন মন্তব্য নিজেই করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। এটি শুধু অস্বস্তিকর নয়, বরং ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্যও অশনিসঙ্কেত।
নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়েও নতুন বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বিএনপি ও মিত্র দলগুলো সরাসরি ভোটের প্রচলিত পদ্ধতির পক্ষপাতী, অপরদিকে জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদসহ কয়েকটি দল চাইছে সংখ্যানুপাতিক বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক ভোটব্যবস্থা। কেউ কেউ আবার আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন চাচ্ছে। এসব বিতর্ক এখন রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভক্তির রেখা স্পষ্ট করছে।
প্রশ্ন হলো, এই সময়ে পদ্ধতিগত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আসলে কতটা জরুরি? রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বলে নির্বাচনের সময় পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক নয়, বরং গ্রহণযোগ্যতা, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করাই বেশি জরুরি। বাংলাদেশে ভোটের সংস্কৃতির ইতিহাসে বড় সমস্যা হল অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করা। এখন যখন প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন পদ্ধতিগত বিতর্ক কিংবা সময় নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অস্থিরতা ডেকে আনার শামিল।
এছাড়া কিছু রাজনৈতিক দল এই মুহূর্তে ভোট পদ্ধতির পরিবর্তন দাবি করে নিজেদের জন্য সুবিধাজনক অবস্থান নিশ্চিত করতে চায় বলেই সাধারণ মানুষ মনে করছে। ছোট দলগুলো আনুপাতিক পদ্ধতির সুবিধা পেতে চাইছে এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে এ ধরনের পদ্ধতিগত রূপান্তরের বাস্তবতাও নেই। এমন পরিবর্তনের জন্য সময়, আলোচনার পরিবেশ ও নির্দলীয় প্রশাসনিক কাঠামো অপরিহার্য, যা এখন অনুপস্থিত।
অন্যদিকে, অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে। সরকার একদিকে বলছে, নির্বাচন নিয়ে প্রলম্বনের কোনো চিন্তা নেই, অথচ তাদের আচরণে অনেক সময় ভিন্ন বার্তা দেখা যায়। সমন্বয়ের অভাব, পরস্পরবিরোধী বক্তব্য এবং কার্যকরী রাজনৈতিক উদ্যোগ না থাকায় রাজনৈতিক আস্থাহীনতা আরও গভীর হচ্ছে।
এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে চাই, সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট সময়সূচি ও নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও প্রস্তুতি জোরদার করা, নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক অবসানে একটি সমঝোতার পরিবেশ তৈরি করা, ভোটারদের আস্থা ফেরাতে প্রচার ও সচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করা, সমস্ত রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সংলাপ ও সমঝোতার পথ খোলা রাখা।
নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। যদি সেই ভিত্তির ওপর ঘনিয়ে আসে অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের মেঘ, তবে তা দেশের রাজনীতি, প্রশাসন ও সমাজব্যবস্থার জন্য সুদূরপ্রসারী ঝুঁকি বয়ে আনতে পারে।
আমরা মনে করি, নির্বাচন নিয়ে অনর্থক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না বাড়িয়ে, অবিলম্বে একটি স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে সবচেয়ে দায়িত্বশীল কাজ।